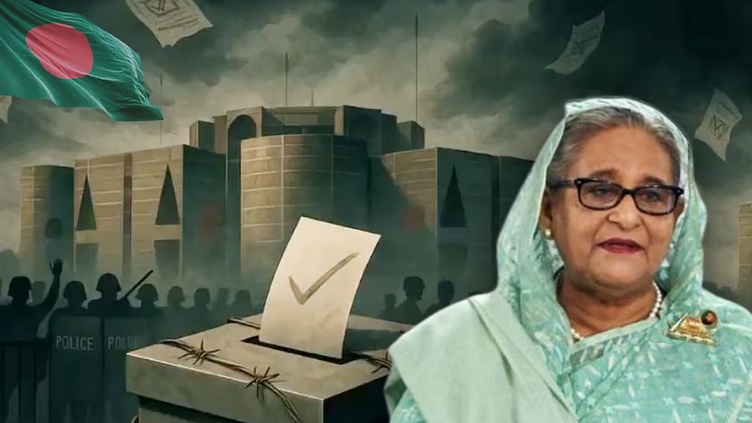কক্সবাংলা ডটকম(১০ অক্টোবর) :: দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন। আর শিশু-কিশোরদের মধ্যে এ হার ১২ দশমিক ৬ শতাংশ। আক্রান্তের এ পরিসংখ্যানের বিপরীতে দেশে সাইকিয়াট্রিস্ট বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা মাত্র ৩৫০ জন। অর্থাৎ দেশে প্রায় প্রতি ছয় লাখ মানুষের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ। এসব তথ্য জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষত তরুণ-তরুণীদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সংকট, মাদকাসক্তি, সামাজিক সম্পর্কের অবনতি, উদ্বেগ, আতঙ্ক, মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা, ডিজিটাল ডিভাইসে আসক্তিসহ বিভিন্ন কারণে নানা বয়সের মানুষ মানসিক রোগের ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের প্রকাশ করা ‘মানসিক স্বাস্থ্য: বাংলাদেশের তথ্যচিত্র-২০২৫’-এ বলা হয়েছে, দেশের মানসিক রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিষণ্নতায় ভোগেন ৬ দশমিক ৭ শতাংশ, উদ্বেগজনিত রোগে আক্রান্ত ৪ দশমিক ৭ শতাংশ।
এছাড়া সোমাটিক সিম্পটম ডিজঅর্ডারে (ব্যথা, দুর্বলতা, ক্লান্তি) ২ দশমিক ৩ শতাংশ, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডারে (ওসিডি) শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, বাইপোলার ডিজঅর্ডারে (মুড বা মনের অবস্থা ওঠানামা করা) শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ, সিজোফ্রেনিয়া ও অন্যান্য সাইকোটিক ডিজঅর্ডারে ১ শতাংশ ও মাদকাসক্তি রোগে আক্রান্ত শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ।
শিশু-কিশোররাও আক্রান্ত হচ্ছে মানসিক সমস্যায়। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের তথ্যমতে, দেশের শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যার মধ্যে শীর্ষে আছে নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার। এ রোগে আক্রান্তের হার ৫ দশমিক ১ শতাংশ।
এটি এক ধরনের মানসিক ও স্নায়বিক সমস্যা, যা সাধারণত শিশু বয়সেই শুরু হয় এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। এরপর যথাক্রমে রয়েছে উদ্বেগজনিত রোগ (অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার), আক্রান্তের হার ৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং কন্ডাক্ট ডিজঅর্ডার, ১ দশমিক ৭ শতাংশ।
শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে আঁচল ফাউন্ডেশন। মানসিক রোগাক্রান্তদের নিয়ে দেশে তথ্যের ঘাটতি আছে জানিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি তানসেন রোজ বলেন, ‘মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রধান যে সমস্যায় পড়তে হয় তা হলো আমাদের হাতে সঠিক তথ্য নেই। এ বিষয়ে কাজ করতে হলে সবার আগে তথ্য দরকার। আমরা দেখছি ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা বেশি মানসিক সমস্যায় ভুগছে। কারণ এখন শিশুরা ডিভাইসের প্রতি বেশি আসক্ত। তাদের শারীরিক কার্যকলাপ, খেলাধুলা কমে যাচ্ছে। অন্যান্য কারণও রয়েছে।’
যে কারো ক্ষেত্রেই মানসিক সমস্যার লক্ষণ দেখামাত্রই চিকিৎসা শুরুর প্রয়োজন বলে জানালেন তানসেন। তার কথায়, ‘প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা শুরু করতে হবে। এজন্য পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। সেখানেই যেন মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটিতে নজর দেয়া হয়। আমাদের দেশে অবস্থা একেবারে ভয়াবহ না হলে চিকিৎসকের কাছে নেয়া হয় না।’
দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ মানসিক রোগে ভুগলেও চিকিৎসাসেবা নিতান্তই অপ্রতুল। রোগী বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়েনি চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কর্মরত জনশক্তি প্রায় প্রতি দুই লাখে একজন। দেশে বর্তমানে মোট সাইকিয়াট্রিস্টের (মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ) সংখ্যা ৩৫০ জন। অর্থাৎ প্রতি প্রায় ছয় লাখ মানুষের বিপরীতে একজন।
‘মানসিক স্বাস্থ্য: বাংলাদেশের তথ্যচিত্র-২০২৫’-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে সাইকোলজিস্ট রয়েছেন ৫৬৫ জন (প্রতি প্রায় তিন লাখে একজন), সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার সাতজন, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ৩২৪, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাধারণ চিকিৎসক ২১ হাজার ২৬৭ জন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ৯ হাজার ৪০০ জন, হাসপাতালে কর্মরত সেবিকা ৭০০ জন, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স ২৮ হাজার ১৬৫ জন, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ১৭২ জন।
মানসিক রোগে আক্রান্ত বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ পান না বলে জানিয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডা. মো. মাহবুবুর রহমান।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশে মানসিক রোগে আক্রান্ত বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে এ চিকিৎসা ব্যবধান প্রায় ৯৪ শতাংশ, যা বিশ্বে গড় ৭০ শতাংশের চেয়েও অনেক বেশি। অন্যদিকে, এ গুরুতর সমস্যা সমাধানে জাতীয় স্বাস্থ্য বাজেটের ১ শতাংশেরও কম বরাদ্দ করা হয়।
এ বড় চিকিৎসা ব্যবধান পূরণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তবে দেশে বর্তমানে ৫০০ জনেরও কম ওয়ার্কিং সাইকিয়াট্রিস্ট রয়েছেন, যা পরিস্থিতিকে আরো কঠিন করে তুলেছে। কর্মজীবীদের মধ্যে মানসিক রোগের আধিক্য না বাড়াতে হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অবশ্যই কর্মীবান্ধব ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি করার ওপর জোর দিতে হবে।’
স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকেও গুরুত্ব দেয়ার কথা বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।
তিনি বলেন, ‘সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কর্মসংস্থান, শিক্ষাব্যবস্থাসহ আরো কিছু খাতে অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে নিরাপত্তা, সম্মানবোধ জাগ্রত হলে অনেক কিছু সুস্থ হয়ে উঠবে। এরই মধ্যে যারা সমস্যার মধ্যে আছেন, তাদের জন্য সমন্বিতভাবে একটা সেবা চালু করা দরকার।
সেটা সরকারি-বেসরকারি উভয়ভাবেই হতে পারে। দেশব্যাপী সাধারণ যে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা যোগ করা যেতে পারে। যোগ্য পেশাজীবীরা থাকলেও তাদেরকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক তারা যেন দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যসেবার দিকেও নজর দেন।’
অনেক ক্ষেত্রেই রোগীরা চিকিৎসা শেষ করতে পারেন না উল্লেখ করে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. সালাহউদ্দিন কাওসার বিপ্লব বলেন, ‘হাসপাতালে বা চেম্বারে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর ওপর ভিত্তি করে আসলে বলা কঠিন কোন ধরনের রোগী বেশি। দেশের বেশির ভাগ মানুষ জানেই না যে তারা মানসিক সমস্যায় ভুগছে।
একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষ মূলত চিকিৎসা নিতে আসে। আর যারা চিকিৎসা নেয় তাদের মধ্যেও ধারাবাহিকতা থাকে না। অর্ধেক চিকিৎসার পর আর কন্টিনিউ করে না। খরচেরও একটি ব্যাপার থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক চিকিৎসা ব্যয়বহুল।’